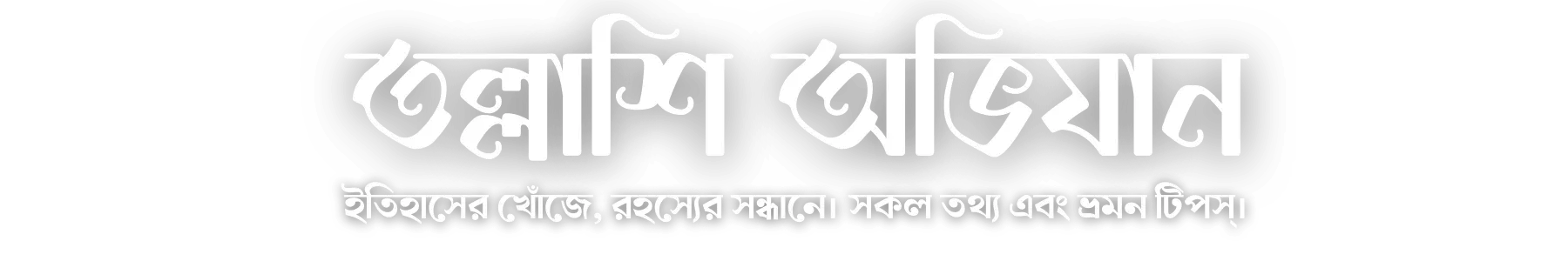বাংলার বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক রাজবাড়ি, অনেক রাজত্বের নিঃশব্দ সাক্ষী। তেমনই এক রাজকীয় নিদর্শন দুবলহাটি রাজবাড়ী। নওগাঁ জেলার সদর উপজেলায় দাঁড়িয়ে আছে এক ইতিহাসের নীরব প্রহরী চলুন, আজ ঘুরে আসি এই রাজ্যের এক বিস্ময়কর অধ্যায়ে।
দুবলহাটি রাজবাড়ী নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। এর স্থপত্যে ফুটে উঠেছে ইউরোপীয় প্রভাব আর বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের অপূর্ব মিশেল।
রাজবাড়ির গায়ে লেগে আছে সময়ের ধুলো, কিন্তু তার প্রতিটি দেয়াল আজও বলে চলে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় গাথা।”
“তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এই প্রাসাদ আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
যেখানে কোনো এক কালে বাজতো সানাই, সেই প্রাঙ্গণে এখন শুধু নীরবতা।”
আমরা যদি আজ ইতিহাসকে সংরক্ষণ না করি, আগামী প্রজন্ম কীভাবে জানবে তাদের শিকড়?
দুবলহাটি রাজবাড়ী শুধু একটি স্থাপনা নয়—এটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি জীবন্ত অধ্যায়।
নওগাঁ জেলার সদর উপজেলা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এই বিশাল প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে।
নির্মাণশৈলীতে ফুটে উঠেছে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ছোঁয়া, যা বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে এক অপূর্ব মিশেল সৃষ্টি করেছে।
রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
এই রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জগৎরাম রায়। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় লবণ ব্যবসায়ী। এখানে ছিল ৩০০টির বেশি কক্ষ, অন্দরমহল, রাজসভার ঘর, অতিথিশালা, এমনকি একটি নাট্যমঞ্চ। একসময় এখানে চলতো জাঁকজমকপূর্ণ সভা, বাজতো সানাই, আর নাচতো নর্তকীরা।
কিন্তু সময় সবকিছু বদলে দেয়। স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে এই রাজবাড়িও হারিয়ে ফেলে তার গৌরব। আজ সে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত এক স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে। নীরব, একাকী… অথচ ইতিহাসের ভারে গম্ভীর।
“আমাদের প্রশ্ন—এই ঐতিহ্যকে কি আমরা রক্ষা করতে পারছি? নাকি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি নিজের শিকড়, নিজের ইতিহাস?”
“আমরা যদি আজ ইতিহাসকে সংরক্ষণ না করি, আগামী প্রজন্ম কীভাবে জানবে তাদের শিকড়?
দুবলহাটি রাজবাড়ী শুধু একটি স্থাপনা নয়—এটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি জীবন্ত অধ্যায়।”
দুবলহাটি রাজবাড়ী কিভাবে যাবেন?
নওগাঁর প্রাণকেন্দ্র, বাসস্ট্যান্ড থেকে মাত্র ২০-২৫ মিনিটের পথ — আর সেখানেই অপেক্ষা করছে এক হারিয়ে যাওয়া রাজত্ব, দুবলহাটি রাজবাড়ী।
কত টাকা ভাড়া লাগবে?
আপনি চাইলে বাসস্ট্যান্ড থেকেই যেকোনো ব্যাটারি চালিত অটোতে উঠে পড়তে পারেন। মাত্র ২০ থেকে ৪০ টাকার ভাড়ায় আপনি পৌঁছে যাবেন এক ঐতিহাসিক যাত্রার গন্তব্যে।
রাস্তায় চলতে চলতেই হঠাৎ চোখে পড়ে প্রাসাদের একাংশ। সত্যি বলতে, প্রথম ঝলকে রাজবাড়ীর সৌন্দর্য দেখে আমরা রীতিমতো মুগ্ধ। ভাবতেই অবাক লাগে — কত শত বছর আগেও মানুষের কল্পনাশক্তি আর নির্মাণশৈলী কতটা উন্নত ছিল!”
প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে একটি বড় পুকুর — ঘাট বাঁধানো, সুন্দর করে গাঁথা। ধারণা করা হয়, এই পুকুরেই গোসল করতেন রাজা ও রানী। এ যেন অতীতের রাজকীয় জীবনের নিঃশব্দ সাক্ষ্য!”
আমরা ভেবেছিলাম প্রধান দরজা দিয়েই প্রবেশ করবো, কিন্তু সেটি বন্ধ! তবে চিন্তা নেই — পাশের একটি কক্ষের ভেতর দিয়ে আপনি সহজেই রাজবাড়ীর ভেতরে ঢুকতে পারবেন।
ভেতরে ঢুকে আপনি দেখতে পাবেন বিশাল দালানকোঠা, আর সময়ের ছাপ লাগা দেয়াল। প্রতিটি ইটে লেখা আছে এক রাজ্যপতির গৌরবগাঁথা।”
“দুবলহাটি রাজবাড়ী আমাদের শুধু ইতিহাস শেখায় না, শেখায় অতীতকে সম্মান করতে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় — রাজারা চলে গেলেও, তাদের ছায়া এখনো সময়ের উপর আঁকা রয়ে গেছে।”
“ভিতরে ঢুকেই আমাদের প্রথম চিন্তা — রাজা-রানীর থাকার সেই রাজকীয় ভুবনটা কোথায়? কোথায় সেই কক্ষ, যেখান থেকে একসময় শাসন চলত, যেখান থেকে ইতিহাস রচিত হতো?”
দুবলহাটি রাজবাড়ী কিভাবে তৈরি হয়?
“সময়টা ১৭৯৩ সাল…
ইতিহাসের পাতায় লেখা এক সাহসী সিদ্ধান্ত — মাত্র ১৪ লক্ষ ৪ শত ৯৫ টাকার বিনিময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে পত্তন নেওয়া হয় এক বিশাল জমিদারির। আর সেখান থেকেই শুরু হয় দুবলাহাটি রাজ্যের পথচলা…”
এই জমিদারির সূচনা করেন জমিদার কৃষ্ণনাথ। তবে কপালের লিখন, তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না।
তাই পরবর্তীতে তাঁর কন্যার পুত্র — হরনাথ রায় ১৮৫৩ সালে এই জমিদারির দায়িত্ব নেন। আর এখান থেকেই বদলে যেতে থাকে ইতিহাসের ধারা।
হরনাথ রায়ের আমলেই দুবলাহাটি রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তিনি শুধু রাজত্ব চালাতেন না — তিনি ছিলেন রুচিশীল, প্রজাবান্ধব এবং সংস্কৃতিপ্রেমী এক শাসক। প্রজাদের সুপেয় জলের অভাব দূর করতে তিনি রাজপ্রাসাদের চারপাশে খনন করান বহু পুকুর। নির্মাণ করেন অপূর্ব নাট্যশালা, যেখানে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হতো নাটক ও যাত্রাপালা।
তাঁর এবং তাঁর পুত্র কৃঙ্করীনাথ রায় চৌধুরীর সময় ছিল দুবলাহাটি রাজবাড়ির স্বর্ণযুগ। প্রাসাদের বাইরেই গড়ে ওঠে দীঘি, মন্দির, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং এমনকি একটি বিশাল ১৬ চাকার রথও তৈরি হয়, যা আজও ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী।
কেন এই জমিদার বাড়িকে দুবলহাটি রাজবাড়ি বলা হয়?
এই রাজবাড়ির নাম দুবলহাটি, তবে অনেকেই একে ‘দুবলহাটি রাজবাড়ী’ নামেও ডাকেন। কিন্তু এই ‘রাজবাড়ী’ শব্দটির কোনও সরাসরি ইতিহাস কি পাওয়া যায়? না, ঠিক তেমনটি নয়।
ধারণা করা হয়, যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ জমিদারদের দেখেছে এক রাজা-বাদশার চোখে।
তাঁরা ছিলেন প্রতাপশালী, দানশীল, এবং জনপদের অভিভাবক। আর সেই শ্রদ্ধা, সেই বিশ্বাস থেকেই হয়তো এই জমিদার বাড়িটিকে ‘রাজবাড়ী’ নামেই ডাকতে শুরু করে সবাই।
কোনটা রাজপুরুষদের কক্ষ? আর কোনটা রানীদের আবাস?
“প্রতিটি ভবন দেখে যেন একটাই প্রশ্ন মাথায় আসে — কোনটা রাজপুরুষদের কক্ষ? আর কোনটা রানীদের আবাস?
ভবনগুলো এতটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত যে বোঝার উপায়ই নেই কোনটা কী ছিল। তবে একটি বিশেষ ভবনের নকশা দেখে মনে হলো — এটাই হয়তো ছিল রানীদের জন্য নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ।
এবার চলুন, আমরা উঠবো ভবনের দ্বিতীয় তলায়। এই সিঁড়িটি ব্যবহার করে ঘুরে ঘুরে উঠতে হবে উপরে। আর কী আশ্চর্য অনুভূতি — এই পথে একদিন রাজা-রানীরাও হেঁটে উঠতেন!
সিঁড়িটির নির্মাণশৈলী অসাধারণ — সরু, কিন্তু মজবুত। যদিও এখন সেটা সময়ের ভারে ক্লান্ত।
বিশেষ সতর্কতা: যদি আপনি বর্ষাকালে আসেন, দয়া করে সাবধানে চলুন। কারণ ভেজা সিঁড়ি খুবই পিচ্ছিল হয়ে যায় — পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
দ্বিতীয় তলায় উঠে প্রথমেই চোখে পড়লো একটি বিশাল কক্ষ। তবে আজ আর সেই কক্ষের পুরনো সৌন্দর্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। চারপাশে দেয়াল ছিল — সেটা শুধু কল্পনায় আঁকা যায়, কারণ এখন শুধু ধ্বংসস্তূপ আর শূন্যতা।”
এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হয় — এখানে হয়তো কোনো এক সময় রানীরা চাঁদের আলোয় গল্প করতেন, শিশুদের কোলে নিয়ে দোল খেতেন, বা শাড়ির কুণ্ডলি গুটিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।
একটা কষ্টের কথাও বলতে হয় — ইতিহাস যতটা সুন্দর হোক না কেন, সেটা যদি আমরা সংরক্ষণ না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু ধ্বংসাবশেষই পাবে।
এই রাজবাড়ীর প্রতিটি সিঁড়ি, প্রতিটি দরজা, প্রতিটি দেয়াল — একেকটা যেন ইতিহাসের জীবন্ত পৃষ্ঠা। আপনি যদি কল্পনায় দেখতে পারেন, তাহলে চোখ বন্ধ করলেই হয়তো শুনতে পাবেন রাজবাড়ীর প্রাচীন ধ্বনি।
রাজবাড়ির ছাদ
এবার আমরা উঠে যাচ্ছি রাজবাড়ির ছাদে…
আর ছাদে উঠতেই যেন চোখের সামনে উন্মোচিত হলো এক বিস্ময়কর দৃশ্য! চারদিক জুড়ে শুধু সবুজ জঙ্গল আর ধ্বংসের ছাপ। ছাদ থেকে পুরো রাজবাড়ীটা একনজরে দেখা যায়। ঠিক তখনই মনে হলো—এত বিশাল, এত সুন্দর একটি প্রাসাদ… আজ কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে।
এখান থেকে মিনারটি স্পষ্ট দেখা যায়। মিনারের সৌন্দর্য আজও বলে যায়, একসময় এই প্রাসাদে ছিল রাজকীয় শাসনের ছাপ। কিন্তু যেদিকে তাকাই, দেখি কেবল ঝোপঝাড় আর গাছগাছালি। এক সময় এখানে ছিল সাজানো বাগান, রাজকীয় আনাগোনা আর প্রাণের স্পন্দন। আজ সেটা পরিণত হয়েছে নীরব এক জঙ্গলে।
মনটা ভার হয়ে যায়, এত বিশাল একটি রাজবাড়ি, অথচ এখন দেখাশোনার জন্য কেউ নেই।
কোনো সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই, সংস্কারের চিহ্নও নেই। সরকার চাইলে এটিকে সহজেই একটি পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তর করতে পারত। কিন্তু আমরা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের ইতিহাসকে অবহেলায় হারিয়ে ফেলছি।
এরপর আমরা চললাম আরেকটি ভবনের দিকে। আমি একটু সামনে এগোতেই সবাই আমাকে থামিয়ে দিল। কারণ সামনের জায়গাটি এতটাই জঙ্গলে ঢাকা ছিল যে, যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। কেউ বলল—ওদিকটায় নাকি অনেক সাপ দেখা যায়। তাই আমাকে আর কেউ যেতে দিল না।
এই ভবনের কক্ষগুলো দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, বহু বছর ধরে এখানে মানুষের পা পড়েনি। ছোট ছোট ঘর, ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সবকিছু। এই কক্ষগুলো কী উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, তা এখন বোঝা দুঃসাধ্য।
রহস্যময় কক্ষ
তবে হঠাৎ আমরা এমন এক কক্ষে পৌঁছালাম, যেটি দেখে শরীর শিউরে উঠলো! এতটাই অন্ধকার আর গা ছমছমে পরিবেশ—মনে হচ্ছিল যেন এটি একটি বন্দিশালা।
এই কক্ষে দাঁড়িয়ে মনে হলো—একজন মানুষ যদি এখানে থাকেন, তাহলে দিন-রাতের পার্থক্যও টের পাবেন না। কোনো আলো প্রবেশ করে না, জানালা নেই, বাতাসও যেন আসে না।
স্থানীয়দের অনেকে বলেন, এই কক্ষে নাকি এক সময় বন্দীদের আটকে রাখা হতো। তবে সেই ইতিহাস কতটুকু সত্য, তার সঠিক প্রমাণ আমরা পাইনি।
কিন্তু এই কক্ষের পরিবেশ, নিঃসঙ্গতা আর অন্ধকার… মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস শুধু গল্প নয়, একেকটা কক্ষ একেকটা নিরব সাক্ষী।”
“রাজবাড়ীর প্রতিটি ইট যেন চিৎকার করে বলছে—আমাদের কথা কেউ শুনছে না। আমরা ইতিহাসের ভার বয়ে চলেছি, অথচ আমাদের কেউ যত্ন নিচ্ছে না।
আপনারাই বলুন, এই রাজবাড়ী কি সংস্কারের দাবিদার নয়?
হরনাথ রায় কিভাবে খাজনা দিতেন?
আরও একটি অদ্ভুত সত্য ঘটনা আছে। যখন জমিদার হরনাথ রায় তার জমিদারির পরিসর দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলছিলেন — তখন সেই খবর পৌঁছে যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কানে।
নবাব এক চিঠি পাঠান হরনাথের উদ্দেশে। প্রশ্ন করেন — তোমার রাজ্যে এত সম্পদ, এত জমি — কিন্তু তুমি খাজনা দাও না কেন?
হরনাথ রায়ের জবাব ছিল অকপট —আমার জমিতে ধান হয় না নবাব, আমার রাজ্যে শুধু বিল আর জলাভূমি। এখানে ফসল নয়, জন্মায় মাছ… আর সেই মাছই আমার সম্পদ।
তবে চাইলে বছরে বছরে কৈ মাছ দিতে রাজি আছি।” নবাব সেই প্রস্তাবে রাজি হন। আর নির্ধারণ করা হয় — খাজনা হিসেবে প্রতিবছর ২২ কাউন্ট কৈ মাছ দিতে হবে।
২২ কাউন্টে হিসাবটা পরিস্কার করে দিন ১ কাউন্ট সমান ১২৮ পিস। ২২ কাউন্ট মানে ২৮১৬টি। কর হিসেবে কৈ মাছ দেওয়ার ঘটনা গিনিসবুকে রেকর্ড হয়েছে।
রাজবাড়ীর বিচার ব্যবস্থা
আমরা একটু সামনে এগোতেই চোখে পড়ল, রাজবাড়ির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল গেট।
প্রথম দেখাতেই মনে হলো, এ গেট কেবল প্রবেশের পথ নয়, এ যেন ক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক।
এর নকশা, খোদাই আর শিল্পের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে দেয় মুহূর্তেই। মনে হয়, ঠিক এই জায়গাতেই বসে
জমিদার তার এলাকার সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন, শুনতেন মানুষের অভিযোগ, দিতেন বিচার।
গেটটির প্রতিটি খুঁটিনাটি অতীতের মহিমা আর জমিদারি শাসনের গৌরব চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলে।
রাজবাড়ির অবকাঠামোর
এবার চলুন জেনে নিই এই ঐতিহাসিক রাজবাড়ির অবকাঠামোর গল্প। কি দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই বিশাল স্থাপনা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছে গর্বের সাথে?
বালি ও চুন
প্রথমেই বলি, রাজবাড়ির মূল কাঠামো গড়ে উঠেছিল অসংখ্য শক্তপোক্ত ইট দিয়ে।
এই ইটগুলোকে একসাথে বাঁধতে বালির সাথে সিমেন্ট নয়, ব্যবহার করা হয়েছিল চুন। যা সেই সময়ের অন্যতম প্রধান নির্মাণ উপকরণ ছিল।
কাঠ
আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল বিশাল আকৃতির কাঠ,
বিশেষ করে বিম বা সাপোর্ট হিসেবে। দুই শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও সেই কাঠ আজও অটুট,
যা প্রমাণ করে সেই যুগের কাঠ কতটা শক্তিশালী ও টেকসই ছিল।
পাথর
এছাড়াও, রাজবাড়ির সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যবহৃত হয়েছিল পাথর। বিশেষ করে বাগানের পথ, সিঁড়ি ও কিছু অলংকৃত স্থাপনায়।
লোহার পাথ
উপরে ছাদে বসানো হয়েছে বিশাল, রেললাইনের মতো দেখতে লোহার পাথ। প্রতিটি এতটাই ভারী যে একা সরানো প্রায় অসম্ভব। আমি নিজেও চেষ্টা করেছি— ফল শূন্য। চাইলেই আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তখনই বুঝবেন কতটা শক্ত ও ভারী এই লোহার কাঠামো।
এর উপর সাজানো হয়েছে ছোট ছোট টাইলসের মতো পাথর, যা সূক্ষ্ম নকশায় বসানো। সূর্যের আলো বা বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে, এই টাইলসের সৌন্দর্য যেন আরও ফুটে ওঠে। যেন শত বছরের পুরোনো এক শিল্পকর্ম, যা আজও চোখ জুড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেগুলো অযত্নে অবহেলা ধসে পরছে।
শেষ মন্তব্য
যানিনা… আজ থেকে ১০ কিংবা ১৫ বছর পর এই রাজবাড়ি আদৌ থাকবে কিনা। হয়তো তখন দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু কিছু ভাঙা দালান, ধসে পড়া ইটের স্তূপ। যা একসময় ছিল আমাদের গৌরবের প্রতীক।
এই রাজবাড়ি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। কিন্তু আমরা, আমরা নিজের হাতেই যেন ধ্বংস করছি আমাদের ইতিহাস। হারিয়ে ফেলছি আমাদের শেকড়, আমাদের পরিচয়।