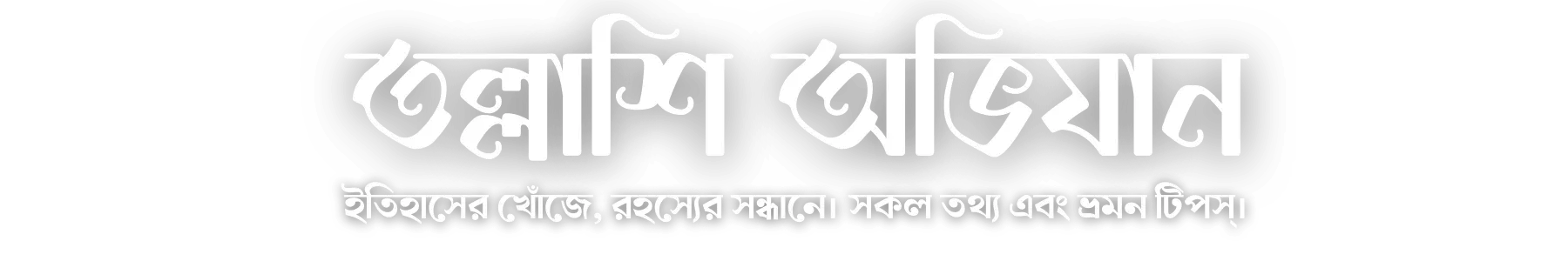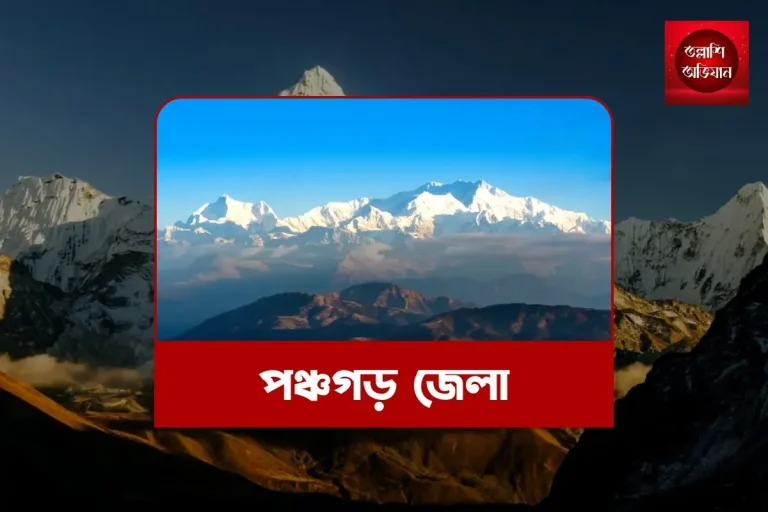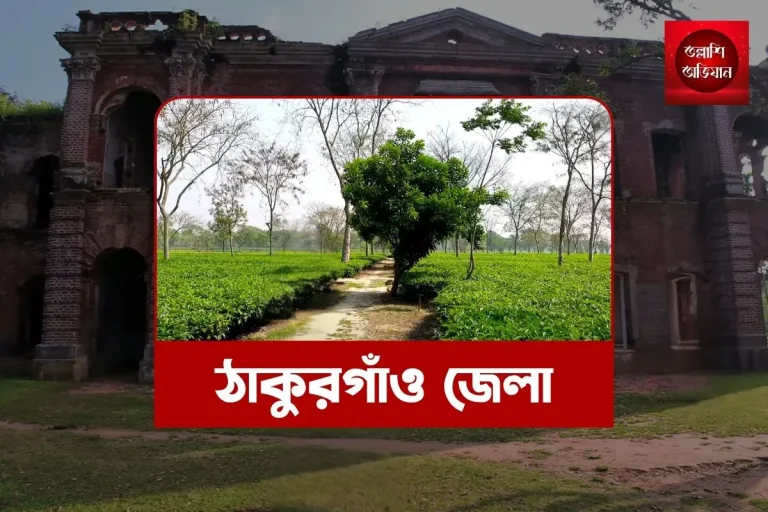তিস্তা নদী হলো বাংলাদেশ ও ভারতের এক যৌথ জীবনধারা — একে শুধু একটি নদী বললে কম বলা হয়। ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পাহাড় বেয়ে বয়ে এসে এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে।
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসেবে তিস্তা হলো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদী নম্বর ৫২।
উৎস ও ব্যুৎপত্তি
“তিস্তা” নামের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ ত্রিস্রোতা বা “তিন প্রবাহ” থেকে। সিকিম হিমালয়ের প্রায় ৭,২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত চিতামু হ্রদ থেকে এই নদীর জন্ম।
সেখান থেকে এটি দার্জিলিংয়ের ঘনবন আর পাহাড়ি গিরিখাত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। এরপর নীলফামারীর কালীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।
ঐতিহাসিক পটভূমি
একসময় তিস্তা নদী গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭৮৭ সালের ভয়াবহ বন্যা এর গতিপথই পাল্টে দেয়। সেই বন্যার পর তিস্তা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে গিয়ে আজকের মতো লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলমারীতে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে।
বর্তমানে নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১১৫ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত।
ভূগোল ও প্রকৃতি
তিস্তা সিকিমে প্রবাহিত হওয়ার সময় অসংখ্য গিরিখাত ও বনভূমি তৈরি করেছে।
এর উচ্চ অববাহিকায় দেখা যায় আল্পীয় বনভূমি, আর নিম্ন অববাহিকায় ক্রান্তীয় গাছপালা।
নদীর তলদেশে সাদা বালি ও পাথরের স্তর — যা স্থানীয় নির্মাণশিল্পের অন্যতম কাঁচামাল।
তিস্তার জলে বড় বড় বোল্ডার থাকায় এটি র্যাফটিং অভিযাত্রীদের কাছেও এক আকর্ষণীয় গন্তব্য।
নদীপথের পরিবর্তন
১৫০০ সালের পর থেকে তিস্তা বহুবার নিজের পথ পরিবর্তন করেছে।
আগে নদীটি তিনটি ধারা — করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা — দিয়ে প্রবাহিত হতো।
এই “তিন স্রোত” থেকেই এর নাম হয়েছিল ত্রিস্রোতা, পরে বিকৃত হয়ে তিস্তা।
কিন্তু ১৭৮৭ সালের বন্যার পর এটি নতুন খাতে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে, আর পুরনো খাতটি এখন বুড়ি তিস্তা নামে পরিচিত।
তিস্তা নদী ও জলবণ্টন সমস্যা
তিস্তা নদী শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস নয়, দুই দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েনেরও প্রতীক।
১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি হয় —
বাংলাদেশ পাবে ৩৬%, ভারত পাবে ৩৯%, আর বাকী ২৫% থাকবে নদীর জন্য সংরক্ষিত।
কিন্তু বাস্তবে ভারতের গজলডোবা বাঁধ নির্মাণের পর বাংলাদেশের অংশে তিস্তার জলপ্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
২০১৪ সালে শুষ্ক মৌসুমে নদীটির জলপ্রবাহ একেবারে শূন্যে নেমে আসে —
ফলে ১২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা অববাহিকায় মানুষের জীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, তিস্তা দিয়ে উভয় দেশ মিলিয়ে প্রায় ১৬ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এখন তিস্তার পানিপ্রবাহ এতটাই কম যে এই পরিকল্পনা অনেকটাই অনিশ্চিত।
তিস্তা আজ
বাংলাদেশ অংশে এখন অনেক জায়গায় তিস্তায় দেখা যায় বালুর স্তূপ, শুকনো চর, আর মাঝে মাঝে ভয়াবহ ভাঙন।
প্রতিবছর শত শত পরিবার হারায় ঘরবাড়ি, চাষের জমি ও জীবিকা।
তবুও, বর্ষা নামলেই তিস্তা আবারও প্রাণ ফিরে পায়, গর্জন তোলে — যেন মনে করিয়ে দেয়, সে এখনো জীবিত, শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটু ন্যায্য জলের অপেক্ষায়।
উপসংহার
তিস্তা নদী শুধু এক জলধারা নয় — এটি দুই দেশের ইতিহাস, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।
তিস্তা যদি বাঁচে, তাহলে বাঁচবে উত্তরবঙ্গের লাখো মানুষের জীবন ও জীবিকা।
এই নদীর ন্যায্য জলপ্রবাহ নিশ্চিত করাই হতে পারে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এক সবুজ প্রতিশ্রুতি।
FAQ
১. তিস্তা নদীর উৎস কোথায়?
উত্তর: তিস্তা নদীর উৎপত্তি ভারতের সিকিম রাজ্যের হিমালয় পর্বতমালার প্রায় ৫,৩৩০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সো লামো হ্রদ থেকে। এরপর এটি দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি অতিক্রম করে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার কালীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশ করে।
২. তিস্তা নদীর নাম “তিস্তা” কেন?
উত্তর: “তিস্তা” নামটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘ত্রিস্রোতা’ বা “তিন প্রবাহ” থেকে। একসময় নদীটি তিনটি ধারায়— করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা — প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে উচ্চারণে পরিবর্তন হয়ে ত্রিস্রোতা থেকেই “তিস্তা” নামটি গঠিত হয়।
৩. তিস্তা নদী কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত?
উত্তর: তিস্তা নদী একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এটি ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করে বাংলাদেশের রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে।
৪. তিস্তা নদীর জলবণ্টন সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তর: ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গজলডোবা বাঁধ নির্মাণের পর তিস্তার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ কমে যায়। এর ফলে বাংলাদেশের অংশে শুষ্ক মৌসুমে নদী প্রায় শুকিয়ে যায়।
যদিও ১৯৮৩ সালের চুক্তিতে জল ভাগাভাগির প্রস্তাব ছিল, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি—ফলে দুই দেশের মধ্যে এখনো এই বিষয়ে সমঝোতা হয়নি।
৫. তিস্তা নদীর গুরুত্ব কী?
উত্তর: তিস্তা নদী উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, কৃষি ও পরিবেশের প্রাণরেখা। এই নদীর পানি দিয়ে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব।
তাছাড়া নদীটি সীমান্ত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি ও পর্যটনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ — তাই একে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের “জীবনরেখা” বলা হয়।